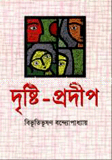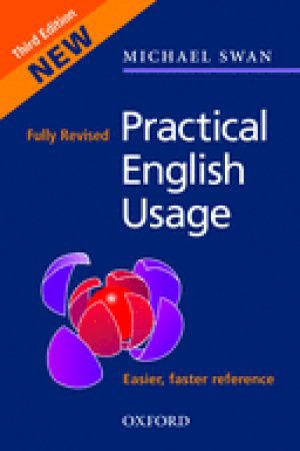উপন্যাসের মূল চরিত্র আবদুল্লাহ। বি.এ পরীক্ষার অল্প কয়েক মাস বাকী। এমন সময় পিতার মৃত্যুতে পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল।
আব্দুল্লাহর জন্ম প্রভাবশালী পীরবংশে। গ্রামের নাম পীরগঞ্জ। অতীতে গ্রামের চারদিকের বহু গ্রামে এ বংশের মুরিদ ছিল। বর্তমানে মুরিদের সংখ্যা কয়েক ঘর মাত্র। কাজেই পীর হিসেবে আব্দুল্লাহর পিতার উপার্জন সামান্যই ছিল। এই সামান্য আয় দিয়ে তিনি ছেলেকে কলকাতায় রেখে লেখাপড়া করাচ্ছিলেন।
আব্দুল্লাহর পিতা পৈতৃক খোন্দকারী ব্যবসায়েই ছিলেন। তবে তিনি বুঝেছিলেন যে ইংরেজি না শিখলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা ঘুচবে না। এদিকে তিনি এও স্পষ্ট দেখছিলেন যে, ইংরেজি যারা শেখে তাদের ইসলামী আকিদা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই তার পরিকল্পনা ছিল প্রথমে ছেলেকে মাদ্রাসায় পড়িয়ে, তারপর ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করবেন।
কিন্তু আব্দুল্লাহ মাঝপথে মাদ্রাসা ছেড়ে দিয়ে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়ে যায়। সন্তুষ্ট না হলেও তার পিতা আপত্তি করেন নি। বরং পুত্র ইংরেজি পড়ে উঁচু দরের চাকরি পাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ উপার্জন করবে এমন আশা আব্দুল্লাহর পিতামাতা উভয়েই করেছিলেন।
তাছাড়া আব্দুল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, পাকা মুসল্লীর মতই সকল বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে চলে। কাজেই ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে পুত্র যদি বড়লোক হয়, তাতে তারা কেন বাধা দেবেন? আব্দুল্লাহর পিতা-মাতা বাধা দেয় না। বরং তারা স্বচ্ছল দিনের অপেক্ষা করতে থাকে।
কিন্তু এমন সময় পিতার মৃত্যুর জন্য আব্দুল্লাহ প্রস্তুত ছিলো না। পিতার মৃত্যুর সাথে সাথে খোন্দকারি উপার্জনও বন্ধ হলো।
পুত্রের মাদ্রাসা ছেড়ে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হওয়া তার পিতামাতা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ পীর-মুরিদি পেশায় আসীন হতে রাজি ছিলো না। তাতে যদি অন্য উপার্জনের চেষ্টা করতে গিয়ে তার পড়ালেখা বন্ধ হয় তা মানতে সে বরং রাজি ছিলো।
মায়ের অনুরোধে নিজ শ্বশুরের কাছে সাহায্য প্রার্থনার জন্য যাত্রা শুরু করে আবদুল্লাহ। এই যাত্রার মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরের চরিত্রগুলো একে একে উন্মোচিত হতে থাকে। সেই সাথে গল্প এগিয়ে যেতে থাকে আর পাঠকের কাছে একে একে ফুটে ওঠে সেই সময়ের মুসলমান সমাজের ভেতরকার নানা ধরনের দ্বন্দ্ব, বিপরীত ঝোঁক, দ্বিধা এবং কুসংস্কার।
কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর যখন তাহার মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তখন নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা কথা মনে উঠিতে লাগিল। এতদিন সে যে উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহা সফল হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, ক্লান্তদেহে আজ বটবৃক্ষতলে বসিয়ে সে মনে মনে ভবিষ্যতের যে চিত্রটি আঁকিতে ছিল, তাহা নিতান্ত উজ্জ্বলতাহীন নহে।
সকল চরিত্রগুলোর মধ্যেই যে বিষয়টি অবধারিতভাবে ফুটে ওঠে তা হলো পুরাতন ও নতুনের দ্বন্দ্ব, পুরাতন ধ্যান-ধারণা ও আধুনিক ধ্যান-ধারণার মধ্যকার দ্বিধা। ইসলাম-ভীরু মানুষের পরিবর্তনহীনতা এবং নানা ধরনের বৈপরীত্ব আর একই সাথে নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত আব্দুল্লাহর চিন্তার দ্বন্দ্ব।
উপন্যাসটির গুরুত্ব দুই দিক থেকে।
প্রথমত উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে বাংলাভাষী মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিত্র পাওয়া যায় এখানে।
আবার একইভাবে, ব্রিটিশ শাসনের অধীনে সমাজ যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলো সে সময়ের মূল্যায়ন পাওয়া যায় আবদুল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গীতে।
আব্দুল্লাহ উপন্যাসের লেখক কাজী ইমদাদুল হক আব্দুল্লাহর মতন প্রতিকূলতার শিকার হন নি। তিনি দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং পেশাগত জীবনে শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক ও অধ্যক্ষ হিসেবে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। যার স্বীকৃত তিনি পেয়েছেন সরকার থেকে যথাক্রমে খান সাহেব ও খান বাহাদুর খেতাব অর্জনের মাধ্যমে।
আব্দুল্লাহ মূলত লেখক কাজী ইমদাদুল হকের মতো ব্রিটিশ শাসনের অধীনে সেই সময়ের শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চশিক্ষিত এবং পেশাজীবনে সফল ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করে। যারা ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝেছেন কিন্তু ইসলামী বিশ্বাসকে ত্যাগ করেন নি। ফলে স্বভাবতই সমাজ বাস্তবতার ভেতর তারা লক্ষ্য করেছেন নানা ধরনের স্ববিরোধ এবং দ্বন্দ্ব।
সে হিসেবে তৎকালীন সমাজে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে উচ্চশিক্ষিত একজন বাংলাভাষী মুসলমান লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী এবং মূল্যায়ন হিসেবেও এ উপন্যাসের গুরুত্ব রয়েছে।
লেখক পরিচিতি
নির্বাচিত অংশ
আবদুল্লাহ যখন শাহপাড়ায় গোলদার-বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। সংবাদ পাইয়া গৃহস্বামী কাসেম গোলদার ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল এবং তাহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুরাজি ভূলুণ্ঠিত করিয়া আবদুল্লাহর কদমবুসি করিতে উদ্যত হইল। এ ধরনের অভিনন্দনের জন্য আবদুল্লাহ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। পথে হঠাৎ সাপ দেখিলে মানুষ যেমন এক লম্ফে হটিয়া দাঁড়ায়, সেও তেমনি হটিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, আহা, করেন কি, করেন কি, গোলদার সাহেব। (পরিচ্ছেদ ৩)