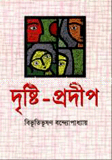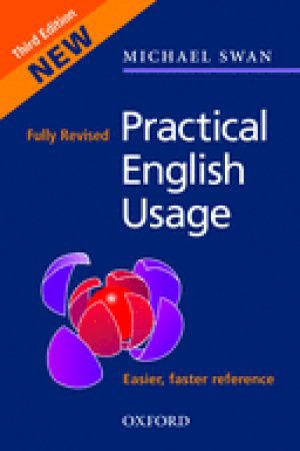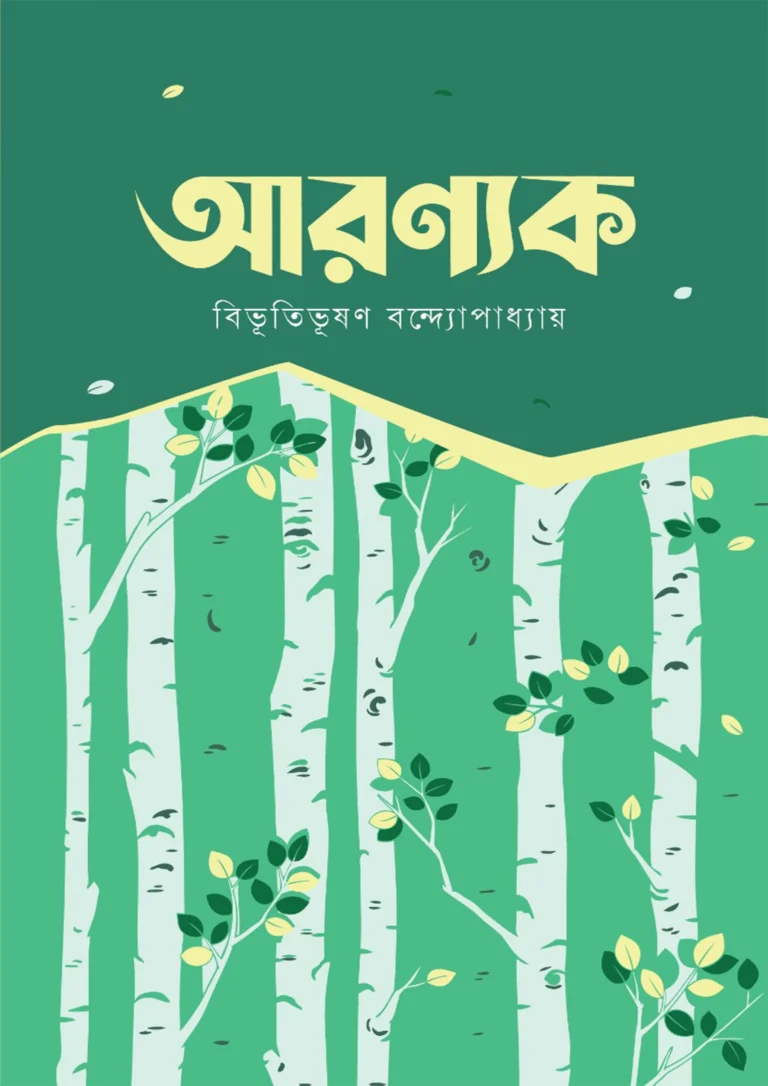পালামৌ উনিশ শতকে লেখা একটি ভ্রমণ কাহিনী। পালামৌ বা পলামু মূলত ঝাড়খণ্ডের একটি জেলা। লেখক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তরুণ বয়সে তৎকালীন পালামৌ পরগণা ভ্রমণ করেন। বইটি তার সেই পালামৌ ভ্রমণের কাহিনী।
রচনার প্রেক্ষাপট
কাহিনীটি লেখক লেখেন তার বৃদ্ধ বয়সে। যৌবনে তাকে অনেকেই এ কাহিনী লিখতে অনুরোধ করলেও তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নি। তবে এখন কেউ অনুরোধ না করলেও তিনি লিখতে বসেছেন। কারণ লেখকের কথায়, “গল্প করা এ বয়সের রোগ, কেহ শুনুন বা না-শুনুন, বৃদ্ধ গল্প করে।”
তবে বৃদ্ধের গল্প কেবল গালগল্প নয়। তার ভেতরে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলি থাকে। আর সেই ঝুলি থেকে সঞ্জীবচন্দ্র কখনো বের করে এনেছেন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ।
বাঙালীর প্রতিবেশীর প্রতি পরশ্রীকাতরতা সম্পর্কে লেখক লিখেছেন:
বঙ্গবাসীমাত্রই সজ্জন, বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা, যাহা নিন্দা শুনা যায় তাহা কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ, বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভালো কাপড়, ভালো জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য। তাহারা আপনাদে পুত্রবধূকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কার দেয়, কেবল আমাদের পুত্রবধূর মুখভার করাইবার নিমিত্ত। পাপিষ্ঠ, প্রতিবাসীরা! যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসী-পরিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রম-পার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিনদিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে।
পালামৌ-র বর্ণনা
পালামৌ-র বর্ণনা লেখক করেছেন।
অঞ্চলটির নানা দিকেই তিনি আলোকপাত করেছেন। কিন্তু সেই বর্ণনাতে পালামৌ একটা স্পষ্ট রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে এমন নয়। বরং একটা গাঢ় অনুভবের মতন পাঠকের মনের ওপর ভর করে।
এই দিকটির দিকে ইঙ্গিত করেই রবীন্দ্রনাথ পালামৌ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,
পালামৌতে সঞ্জীবচন্দ্র যে বিশেষ কোনো কৌতুহলজনক নূতন কিছু দেখিয়াছেন অথবা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কিছু বর্ণনা করিয়াছেন তা নহে, কিন্তু সর্বত্রই ভালোবাসিবার ও ভালো লাগিবার একটা ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। পালামৌ দেশটা সুসংলগ্ন সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান চিত্রের মতো প্রকাশ পায় নাই, …
পালামৌ শহর নয়। একটি পরগণা। শহর সে অঞ্চলেই নাই। এমনকি একটি গণ্ডগ্রামও নাই। আছে কেবল পাহাড় আর জঙ্গল। পালামৌ পাহাড় ও জঙ্গলের দেশ: “পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। “
পাহাড়
পালামৌ পাহাড়ের দেশ। একইসাথে জঙ্গলের দেশ।
পাহাড়ের গায়ে, নিম্নে সর্বত্র জঙ্গল, কোথাও আর ছেদ নাই। কোথাও কর্ষিত ক্ষেত্র নাই, গ্রাম নাই, নদী নাই, পথ নাই, কেবল বন–ঘন নিবিড় বন।
মহিষ ও কোল
পালামৌ অঞ্চলে কোলদের বাস। আর আছে মহিষ। কোলেরা বন্য জাতি। খর্বাকৃতি। গায়ের রং কালো। কোল পুরুষ, শিশু ও নারীদের সৌন্দর্যের মুগ্ধতা ছড়িয়ে আছে লেখকের লেখায়:
কতকগুলি কোলবালক একত্র মহিষ চরাইতেছিল, সেরূপ কৃষ্ণবর্ণ কান্তি আর কখনো দেখি নাই; সকলের গলায় পুঁতির সাতনরী, ধুকধুকির পরিবর্তে এক-একখানি গোল আরশি; পরিধানে ধড়া, কর্ণে বকফুল; কেহ মহিষপৃষ্ঠে শয়ন করিয়া আছে, কেহ বা মহিষপৃষ্ঠে বসিয়া আছে, কেহ কেহ নৃত্য করিতেছে। সকলগুলিই যেন কৃষ্ণঠাকুর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেরূপ স্থান তাহাতে এই পাথুরে ছেলেগুলি উপযোগী বলিয়া বিশেষ সুন্দর দেখাইতেছিল; চারিদিকে কালো পাথর, পশুও পাথুরে; তাহাদের রাখালও সেইরূপ। এই স্থলে বলা আবশ্যক এ অঞ্চলে মহিষ ভিন্ন গোরু নাই। আর বালকগুলি কোলের সন্তান।
এই কোলদের বর্ণনা করতে গিয়েই লেখক বাংলা শিক্ষার্থী মাত্রেরই অতি পরিচিত একটি প্রবাদসম বাক্য রচনা করেছেন:
যে সকল কোল কলিকাতা আইসেবা চা-বাগানে যায় তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও রূপবান দেখি নাই; বরং কুৎসিত বলিয়া বোধ করিয়াছি। কিন্তু স্বদেশে কোলমাত্রেই রূপবান, অন্তত আমার চক্ষে। বন্যেরা বনে সুন্দর; শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।
অসুরদের কথা
পালামৌ পরগণায় পাহাড়ের ভেতরে অসুরদের বাস। সংখ্যায় তারা অল্প। কোলেদের সাথে বা অন্য কোনো বন্য জাতির সাথে তারা পেরে ওঠে না। শোনা যায় অন্য জাতীয় মানুষ দেখলে তারা লুকিয়ে পড়ে।
পালামৌ থেকে আরও কিছু অংশ
পালামৌ অঞ্চলের এক তেজস্বী যুবকের বাঘ শিকারের ঘটনা বর্ণনা করেছেন লেখক:
পথে দেখি একটি যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে যাইতেছে। আমি ভাবিলাম যখন স্ত্রীলোক সাধিতেছে, তখন যুবার রাগ নিশ্চয় ভাতের উপর হইয়াছে; আমি বাঙ্গালী, সুতরাং এ ভিন্ন আর কী অনুভব করিব। এককালে এরূপ রাগ নিজেও কতবার করিয়াছি, তাই অন্যের বীরদর্প বুঝিতে পারি।
যখন আমি নিকটবর্তী হইলাম তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল, “আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এইমাত্র আমার গোরুকে বাঘে মারিয়াছে।
পালামৌ অঞ্চলের জলের কষ্ট। খুব অল্প কথায় লেখক জল সংগ্রহের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন:
এই অঞ্চলে জলাশয় একেবারে নাই, নদী শীতকালে একেবারে শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, সুতরাং গ্রাম্যলোকেরা এক-এক স্থানে পাতকুয়ার ক্ষুদ্র খাদ খনন করে–তাহা দুই হাতের অধিক গভীর করিতে হয় না–সেই খাদে জল ক্রমে চুঁইয়া জমে। আদ-দশ কলস তুলিলে আর কিছু থাকে না, আবার জল ক্রমে আসিয়া জমে। এই ক্ষুদ্র খাদগুলিকে ‘দাড়ি’ বলে।”
কোলদের নাচের বর্ণনা:
সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম; গ্রামের প্রান্তভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ যুবারা সমুদয়ই আসিয়া একত্র হইয়াছে্ তাহারা ‘খোঁপা’ বাঁধিয়াছে, তাহাতে দুই-তিনখানি কাঠের ‘চিরুনি’ সাজাইয়াছে। কেহ মাদল আনিয়াছে, কেহবা লম্বা লাঠি আনিয়াছে, রিক্তহস্তে কেহই আসে নাই; বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলেই নানাভঙ্গিতে আপন আপন বলবীর্য দেখাইতেছে। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃন্ময়-মঞ্চের উপর জড়বৎ বসিয়া আছে, তাহাদের জানু প্রায় স্কন্ধ ছাড়াইয়াছে। তাহারা বসিয়া নানাভঙ্গিতে কেবল ওষ্ঠক্রীড়া করিতেছে। আমি গিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম।
বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল; যদি দেহের কোলাহল থাকে, তবে যুবতীদের দেহে সেই কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমার চক্ষে নূতন; তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেউ চলে না; দোলে না, টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল।
বইয়ের নাম: পালামৌ
লেখক: সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ: বাংলা ১৩৫১ (১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ)
বইটি সংগ্রহ করুন